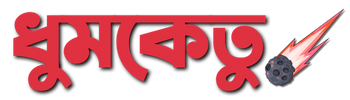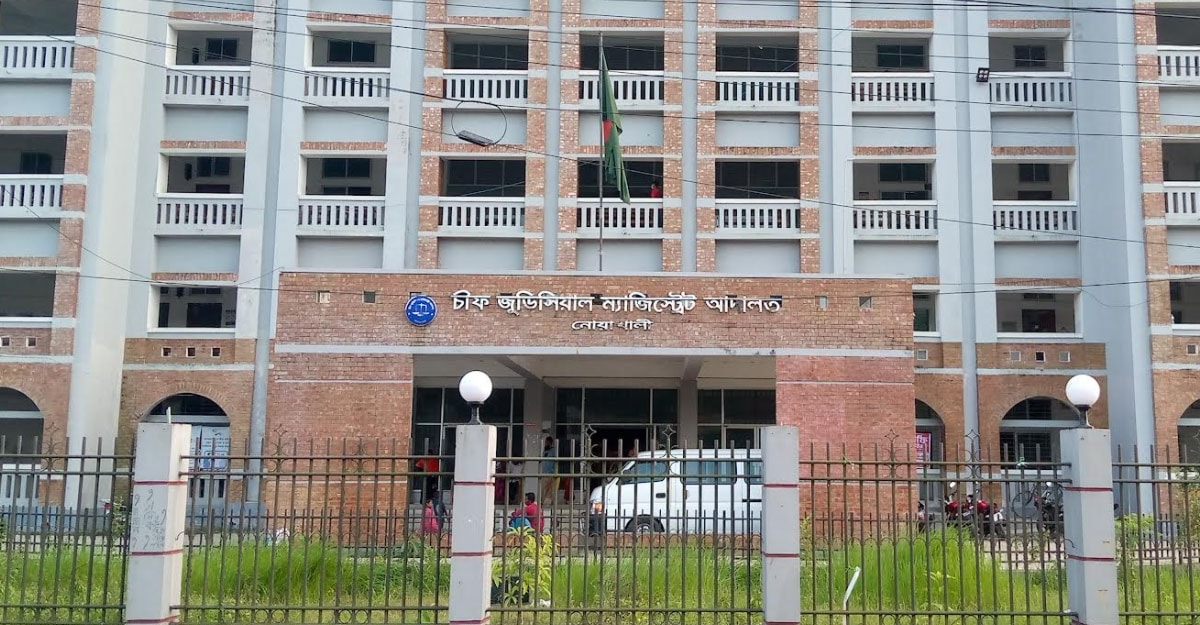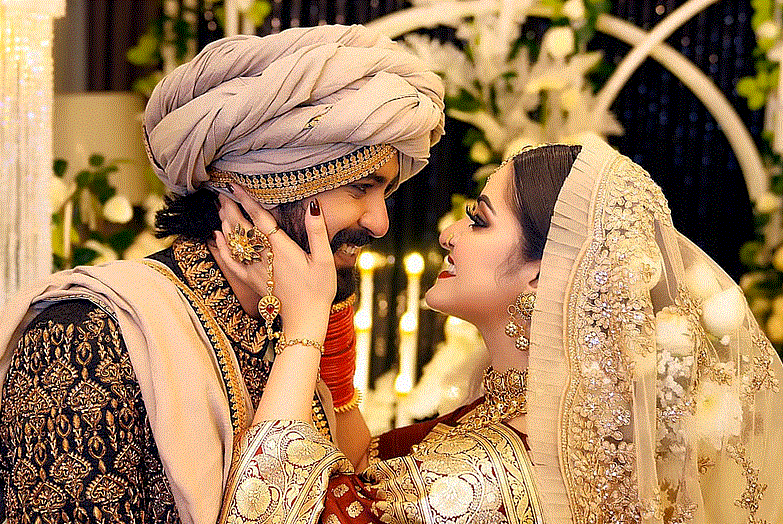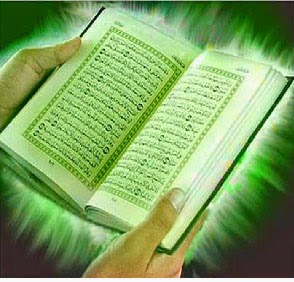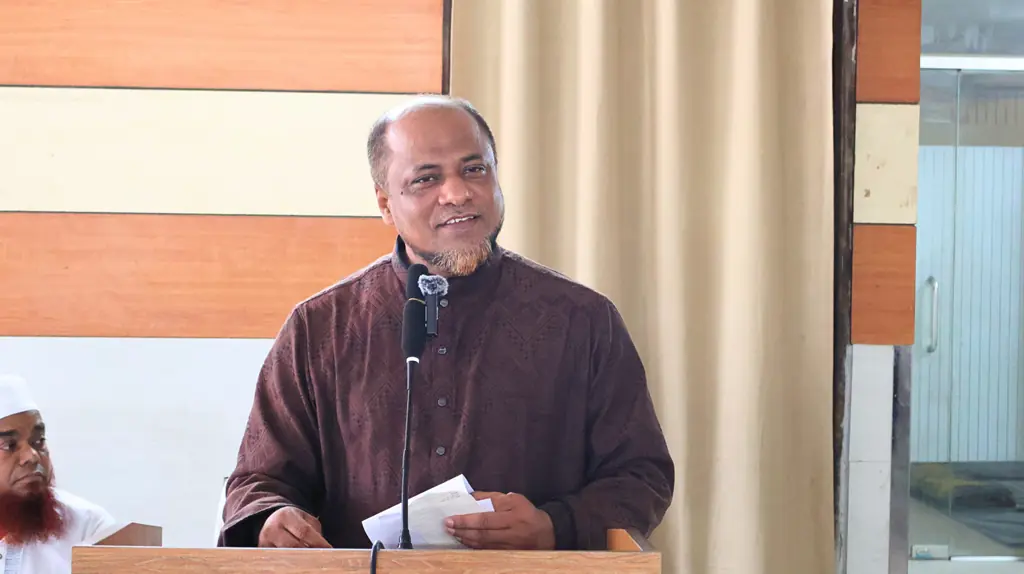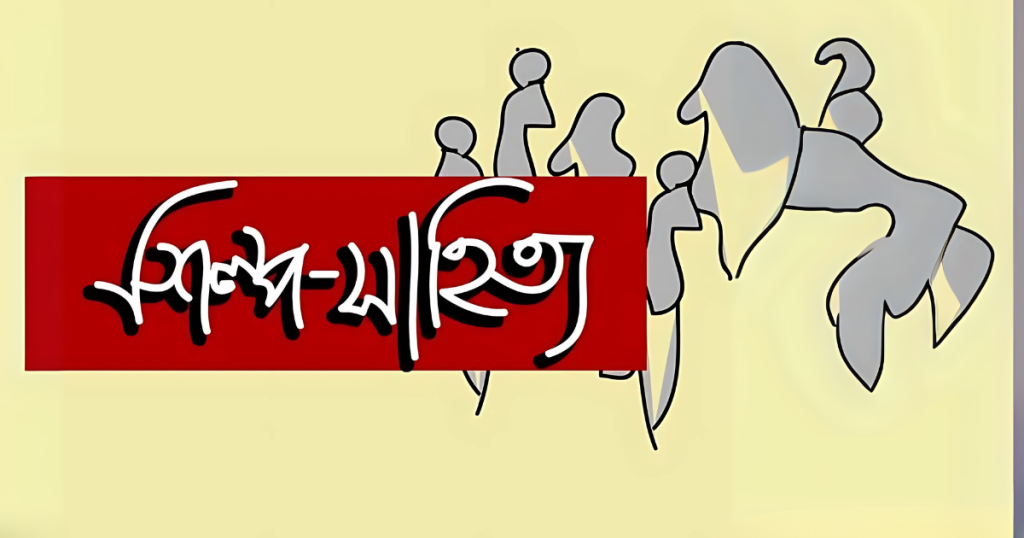
সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা–মনকে শুধু মুগ্ধ করা নয়, হৃদয়কে জাগিয়ে তোলাও।
যে সব শাশ্বত আদর্শ ও গভীর ভাবধারা কালের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে, সে সব ভাব ও আদর্শ যদি সাহিত্য-শিল্পে রূপলাভ করে, তা যে শুধু সহজে মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে তা নয়, হৃদয়ের পটে কায়েমি-ভাবে দাগ কাটতেও তা হয় সক্ষম এবং এভাবেই গড়ে ওঠে ব্যক্তি-চরিত্র ও মানস।
মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা ইতিহাসের সূচনায় এক একটা লৌকিক ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, দেশভেদে ও কালভেদেও ধর্মাদর্শের ও তার অনুষ্ঠানাদির রূপান্তর ঘটেছে নানাভাবে। আর ধর্মাদর্শকে ভিত্তি করে, ভিন্ন ভিন্ন। ভৌগোলিক পরিবেশে নানা সংস্কৃতি যে দানা বেঁধেছে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।
এ সব ধর্মাদর্শ ও সাংস্কৃতিক রূপায়ণ বিভিন্ন ব্যক্তি ও অনুষ্ঠানে যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে–হয়তো তা নিছক কল্পনা, হয়তো তা চূড়ান্ত বিকৃতি, তবুও সামাজের বৃহত্তর অংশকে এ সবই প্রেরণা দিয়ে এসেছে, জুগিয়েছে জন-মনের খোরাক। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে রামায়ণ, মহাভারত, জাতক কাহিনীর কথা, পুঁথি ও সাহিত্যের বিচিত্র কাহিনী, কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকেরাতুল আওলিয়া বা খ্রিস্টীয় সেন্টদের কথা।
সত্যের চেয়েও সত্যকে কেন্দ্র করে মানুষের অর্থাৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের যে কল্পনার জগৎ গড়ে উঠেছে তার মূল্য ও আকর্ষণ অনেক বেশি, তার প্রভাব ও আবেদনও ব্যাপকতর। গীতা-উপনিষদের চেয়ে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব যে অনেক বেশি কে তা অস্বীকার করতে পারে? রামায়ণ-মহাভারতে আমরা রক্তমাংসের মানুষকেই দেখতে পাই। তাদের পাপ-পুণ্য মানুষেরই পাপ-পুণ্য।
তাই সহজেই তারা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। এখানেই ধর্মগ্রন্থের ওপর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। ধার্মিকের চেয়ে সাহিত্য-রসিক যে মানুষ হিসেবে অনেক বড় এ বিষয়ে বোধ করি দ্বিমত নেই।
ইসলামের ধর্মীয় ও আধা ধর্মীয় ঘটনা ও কাহিনীগুলি এখনো যথাযথভাবে সাহিত্য শিল্পের উপরকণ হতে পারে নি। সামাজিক গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতাই তার বড় কারণ। ফলে সাহিত্য-শিল্পের এ দিকটা উপেক্ষিত ও দরিদ্রই রয়ে গেছে। ধর্মাদর্শ ও ভাবধারা সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে রূপায়িত না হলে তা নেহাত কেতাবি ও মৌখিক বুলিতেই পর্যবসিত হয়ে থাকে। তাই আমাদের তথাকথিত ধার্মিকরাও মানুষ হিসেবে অত্যন্ত খণ্ডিত, ভারসাম্যহারা ও রসবোধহীন।
হিন্দু তার দেব-দেবীকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, নাটকে, নভেলে। নিত্য নতুনভাবে রূপায়িত করে তাকে জীবনের সামগ্রী করে নিতে তার কোনো বাধা নেই। বৌদ্ধরাও তা করতে পারে–বুদ্ধ ও বুদ্ধ-জীবন নিয়ে কত অসংখ্য শিল্প-কলাই না দেশ বিদেশে গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টানরাও তাই করে। খ্রিস্ট ও মেরির জীবন নিয়ে কত অসংখ্য শিল্প যে সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যে কোনো শিল্প-বস্তুর যে প্রেরণা তার রস তথা আনন্দের সম্পর্ক রয়েছে–তাই সহজে তা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে ও নাড়া দেয়।
সৃষ্টির আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। ভক্ত ও ত্যাগীদের জীবন যুগে যুগে শিল্প-সৃষ্টির এক বড় উপাদান যুগিয়ে এসেছে। জনসাধারণ এভাবে শিল্পের মাধ্যমে, আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মহৎ জীবনকে নিজস্ব করে নেওয়ার একটা সুযোগ লাভ করে এবং ধর্ম ও নীতিও এভাবে শিল্পের মাধ্যমে সার্থক হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, শিল্প শুধু জীবনের রূপায়ণ নয়, মহৎ জীবনের প্রতিফলনও।
দক্ষিণ জার্মানিতে খ্রিস্টের শেষ জীবন নিয়ে যে passion play হয়, তাতে খ্রিস্ট জীবনের চরম ত্যাগকে লোকচক্ষুর সামনে রূপ দেওয়া হয় নাটকের আকারে এবং প্রতি দশ বছর অন্তর তা অভিনীত হয়। এ দশ বছর ধরে চলে তার প্রস্তুতি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন এবং দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নাটকে যিনি খ্রিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করবেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে খ্রিস্টের ভাবাদর্শে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করেন এবং এভাবে দীর্ঘ সাধনায় নিজেকে সে ভূমিকার যোগ্য করে গড়ে তোলেন।
আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক হজ্জ্ব করতে ও হযরতের। রওজা শরিফ জেয়ারত করতে মক্কা-মদিনা গিয়ে থাকেন। তাদের একজনও কি হযরতের ভাবাদর্শে জীবন যাপনের এক শতাংশ চেষ্টাও করে থাকেন? হযরতের জীবন ও ভাবাদর্শকে সাহিত্য-শিল্পের রস-রূপ করে দিয়ে, আনন্দের সামগ্রী করে তাদের সামনে কখনো পরিবেশন করা হয় নি ফলে তা হৃদয়ের সিংহদ্বার পর্যন্ত ও পৌঁছতে পারে না। তারা শুধু ধর্মের আদেশটুকুই পালন করে, তাকে হৃদয় মনের বস্তু করে নেয় না, নিতে পারে না।
শিল্প ও সাহিত্যের ভেতর দিয়ে অন্যান্য ধর্মের ভাবুকদের জীবন যেমন অনেকের মন-মানসের ও ধ্যানের বস্তু হয়ে উঠেছে, ইসলামের বেলায় তা হয় নি। ইসলামের মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে ও ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য গড়ে ওঠে নি। গড়ে ওঠে নি নাটক-নভেল। ঐ সব জীবন ও কাহিনী রূপায়িত হয় নি যাত্রা ও অভিনয়ে। তাই হয় নি ঐ সব এখনো জন-চিত্তের খোরাক। কারবালার ঘটনার মতো এমন চমৎকার মহাকাব্য বা নাটকীয় উপাদানও ব্যবহার হতে পারে নি রঙ্গমঞ্চে বা ছায়াছবির পর্দায়।
একদা স্বয়ং মধুসূদন তার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, ‘ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনো বৃহৎ কবির উদ্ভব হইত, হাসান ও তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া কী বিরাট এপিক লেখাই না তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল। সমস্ত জাতির অনুভূতিকে সে নিজের পক্ষে টানিতে পারি। আমাদের এমন কোনো বিষয় নাই।’
এপিক তথা মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়েছে–এখন নাটক-নভেল ও ছায়াছবির যুগ। মহাকাব্যের জন্য যেমন মহা প্রতিভার দরকার, এ সবের জন্য তেমন প্রতিভা না হলেও চলে। কাজেই এ সব উপকরণকে এখন যুগোপযোগী আঙ্গিকেও রূপ দেওয়া যেতে পারে।
মুসলমানদের শিল্প-বোধ ও সৃষ্টি প্রতিভা অন্য কোনো রকমে মুক্তি না পেয়ে তা শুধু মসজিদ ও স্মৃতিসৌধেই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ সবের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তা সাধারণ শিল্পীর সাধ্য ও আয়ত্বের অতীত। ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবনের পরিধিতে শিল্প যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপ-লাভ না করে, বৃহত্তর জীবনে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-শিল্পের জন্য কোনো উপকরণই পুরোনো বা বাসি নয়–আঙ্গিক ও রূপ অর্থাৎ form নতুন হতে পারে। নতুন আঙ্গিকে ও নতুন রূপে বহু পুরোনো উপকরণকেই প্রতিভাবান সাহিত্যিক-শিল্পীরা যে অতি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন, সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই।
[‘সাহিত্য ও শিল্পের উপক্ষিত উপকরণ’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এর দশকে সাহিত্য সাপ্তাহিক মেঘনায়। প্রথম গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় ১৯৬১-তে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনায়।]